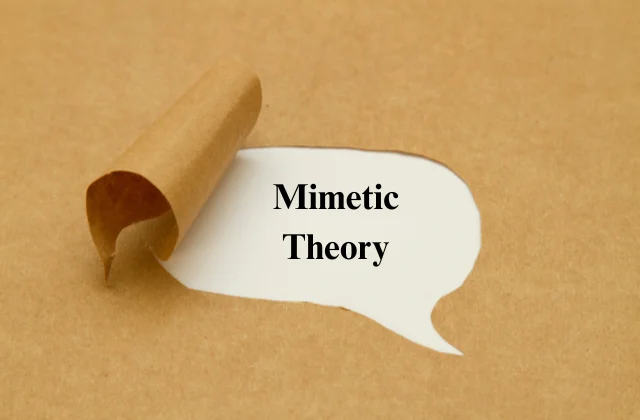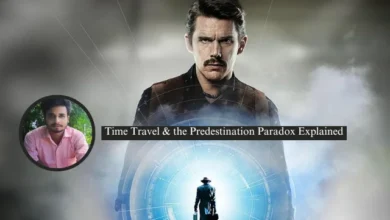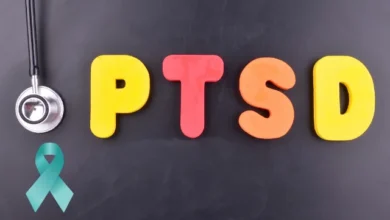মিমেটিক তত্ত্ব: অনুকরণের প্রভাব ও আমাদের আকাঙ্ক্ষার উৎস
ছোটবেলার মুখ ভেংচানো থেকে বড়বেলার স্বপ্ন: রেনে জিরার্দের মিমেটিক তত্ত্বের আলোকে
ছোটবেলায় মুখ ভেংচানোর কথা নিশ্চয় মনে পড়ে। বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং কোন শিক্ষকের কথাগুলো আগে শুনতাম তারপর তার মত করে মুখ ভেংচাতাম। বন্ধুরা সবাই দেখতো আর হাসতো। এরপর কারো কথা বলায় অস্পষ্ট মনে হলে, কারো চলাফেরায় ভুলভাল মনে হলে, আঁকাবাঁকা করে হেঁটে গেলে, ভুল ইংরেজি বললে সেটাও অনুকরণ করে আমরা আমাদের বন্ধুদের শোনাতাম বা দেখাতাম আর নিজেরাও খুব মজা পেতাম, হাসাহাসি করতাম।
আমরা যখন একটু বড় হলাম তখন এই যে ‘অনুকরণ (Mimic)’ করার প্রবণতা আছে সেটাও বড় হতে শুরু করলো। কলেজ জীবনে এসে সেই আমলের তারকাদের মত করে পোশাক-আশাক পরিধান করার চেষ্টা করতাম। তাদের মত করে কথা বলার চেষ্টা করতাম। কোন বন্ধুর হাতে দামি স্মার্টফোন বা দামি হাতঘড়ি দেখে মনে হত, “ইশ্, আমারও যদি ওরকম একটা দামী স্মার্টফোন থাকতো বা দামী হাতঘড়ি থাকতো!” এই নিয়ে আবার বাবা-মায়ের কাছে অনেক অভিযোগ ও অনুরোধ চলতেই থাকতো।
শুধু দামী স্মার্টফোন বা দামী হাতঘড়ি নয়, নির্দিষ্ট স্টাইলের পোশাক, নির্দিষ্ট কোম্পানির সাইকেল বা মোটরসাইকেল নিজের পেতে বা ক্রয় করতে ইচ্ছে করতো। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এটাকে চ্যালেঞ্জ মনে করতো। ফলে তাদের মধ্যে কে কত বেশি নির্দিষ্ট স্টাইলের বা কোম্পানির জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলতো, ঠিক না?
এবার আপনাদের অনেকের একধরণের ‘Bubble (জলবিম্ব/বুদ্বুদ)’ থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করবো। কষ্ট পেতে পারেন কিন্তু বিষয়গুলো যদি সত্য হয় তাহলে আপনাকে এই ‘Bubble’ থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। আমাদের অনেকের মধ্যে এই সমস্যাটা রয়ে গেছে। একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে আমি এই বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করছি।
জনাব ক চান, তার পেশা ওরকম হোক যেরকম টা সবাই করছে। তিনি যেহেতু স্পেশ্যাল সুতরাং তার পেশাও তার চোখে যারা স্পেশ্যাল তাদের মত করে হতে হবে। তিনি চান যখন তিনি তার সহকর্মীদের সাথে আড্ডা দেবেন তখন সবাই তার মত করে চিন্তা করতে সক্ষম হবে। আবার চারপাশে এমন সব বন্ধুদের আজীবন চায়, যারা জ্ঞানীয় যোগ্যতায় তার মত হবে। জনাব ক তার চোখে একটি সুন্দর বাড়ি চান (যে বাড়িগুলো প্রায় একইরকম, কিছু কমবেশি), তার চোখে নির্দিষ্ট কোম্পানির ভালো গাড়ি চান।
বাড়ি-গাড়ি ছাড়াও জনাব ক তার চোখে ভালো নারী চান (নারীদের ক্ষেত্রে নর)। এই নারীর বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে জনাব ক এর ধারণা মোতাবেক। সৌন্দর্য মাপার কিন্তু মাপকাঠি নাই, কিন্তু জনাব ক একজন ফর্সা নারী কে চান বা প্রত্যাশা করেন। জনাব ক মনে মনে জানেন বা ভাবেন, সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে গায়ের রঙে। আর জীবন সঙ্গিনীর মাপকাঠি হচ্ছে তার ধারণা মোতাবেক নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের বাধ্যবাধকতা। এমনকি কোন ধরণের পরিবারে জনাব ক বিয়ে করবেন সেটাও পূর্বনির্ধারিত (জনাব ক এর মনে)।
জনাব ক এমন এক ধরণের মাইনে চান, যে মাইনে দিয়ে পুরো মাস বেশ হাসিখুশিতে কেটে যাবে। শুধু তাই নয়, এই জানুয়ারী মাস শেষেও তার হাতে টাকা থাকবে। তিনি তার ভালো কাজের জন্য সবসময় হাত তালি প্রত্যাশা করেন। মনে মনে ভাবেন, কর্মক্ষেত্র এমন হবে যেখানে তিনি সপ্তাহে ৭ দিন যেতে চাইবেন। আর বাড়িতে ফিরে বউ (মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বামী) এমন হবে যে, বাড়ি থেকে বাইরে পা রাখতে ইচ্ছে করবে না।
আর প্রতিষ্ঠান তার ভালোলাগার দেশগুলোতে নিয়মিত ট্যুর তো দেবেই সাথে একাধিক বোনাসও। সহকর্মীরা শুধু বন্ধু নয়, একেকজন ভাইয়ের মত হবে। আর মাঝখানে যে বন্ধুরা থাকলো? ওহ! তারা চায়ের আড্ডায়/কফিশপে ‘জনাব ক’ কে একদম স্পেশ্যাল অনুভব করাবে। জন্মদিনে ভালো ভালো উপহার দেবে।
জনাব ক এমন এমন সব স্বপ্ন দেখেন যা প্রায় প্রায় কিছু মানুষের মুখে শোনা যায়। কিছু কিছু ব্যক্তি আবার ইতোমধ্যেই তা অর্জন করেছেন। অবশ্য তারাই হলেন ‘জনাব ক’ এর জীবনে রোল মডেল। অবশ্য জনাব ক হুবহু তাদের মত হতে চান না। জনাব ক জানেন বা ভাবেন, তিনি যা স্বপ্ন দেখছেন, তিনি যা প্রত্যাশা করছেন তা ইতোপূর্বে কেউ ভাবেন না। ওসব করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।
ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় জনাব ক যেভাবে যা-কিছু চান আমরাও প্রায় ওরকম জীবন-ই চাই। হ্যাঁ, কিছু কমবেশি বা পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ-ই মোটামুটি আমাদের সবার স্বপ্ন বা প্রত্যাশা। আর আমি এতক্ষণ ধরে যেসব বকবক করছিলাম সেসব মূলত ‘মিমেটিক তত্ত্ব (Mimetic Theory)’ এর মধ্যে পড়ে।
এই ‘মিমেটিক থিওরি (Mimetic Theory)’ হলো ফরাসি দার্শনিক রেনে জিরার্দের (René Girard) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যেখানে তিনি বলেন যে, “মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আসলে স্বতন্ত্র নয়, বরং আমরা অন্যদের অনুকরণ করেই আমাদের ইচ্ছা গঠন করি।” মানে হলো, আমরা ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত যা কিছুই করছি তা কিন্তু একধরণের অনুকরণ ছাড়া নতুন কিছুই নয়।
মানুষ শুধুমাত্র অন্যের থেকে কথা, আচরণ বা পোশাক-আশাক বা বস্তু কেন্দ্রিক বিষয়গুলো অনুকরণ করে না বরং সে অন্যের থেকে তার ‘Desires (ইচ্ছা/বাসনা/আকাঙ্খা)’ -ও অনুকরণ করে থাকে।
বড় হয়ে ছোটবেলার মুখ ভেংচানোর বিষয়টি কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায় না, বরং সুপ্ত থাকে। বড় হয়ে যখন আমরা দেখি আমাদের কোন বন্ধু নির্দিষ্ট কোম্পানির নির্দিষ্ট মডেলের বাইক ক্রয় বা কার ক্রয় করছে আমরা কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট গাড়ি চাইতে পারি। এই চাওয়াটা অপরাধ নয়, এই চাওয়ার পেছনে খেয়াল করলে দেখা যায়, ঐ নির্দিষ্ট গাড়ি নিয়ে যে প্রত্যাশা আমাদের মনে তৈরি হয়েছে তা কিন্তু ওটা আবিষ্কারের আগে ছিলো না।
কিন্তু ওটা যখনই আমাদের মধ্যে কেউ ক্রয় করেছে তখনই আমাদের মনে সেটা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে। আর এটাকেই বলা হয় ‘মিমেটিক ডিজায়ার (Mimetic Desires)’।
প্রশ্ন হলো, আমরা যদি অনুকরণ করি তাহলে সমস্যা ঠিক কোথায়? ‘ChatGPT’ কিন্তু ‘Gemini’ থেকে কপি করে থাকে। আবার ‘Gemini’ কিন্তু ‘ChatGPT’ থেকে কপি করছে বা একধরণের চলমান অনুকরণ/অনুলিপি ঘটছে। এই নয়া নয়া মডেলে নতুন কিছুই মিলছে না। এজন্য সময় সময় মানুষ বিরুক্তও হচ্ছে। হঠাৎ করে ‘DeepSeek’ এসে বাকিদের মার্কেট খেয়ে ফেলছে। কারণ হলো, ‘সৃজনশীলতা’। ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ যদি অন্যের অনুকরণ করতেই থাকে তাহলে মানুষ নিজেকে এবং নিজের ক্ষমতাকে ছোট করছে।
এখানে আরো বড় সমস্যা হচ্ছে, ত্রিভুজ প্রেমের সিনেমার মত। দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা তখনই হবে যখন একটি বস্তুকে একাধিক মানুষ চেয়ে বসবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে আমাদের অধিকাংশের প্রত্যাশা প্রায় একইরকম। আমরা সবাই যদি একটি নির্দিষ্ট চাকুরীর পেছনে ছুটে চলি তাহলে টেকনিক্যালি সবার চাকুরী জুটবে না। হতে পারে ঐ নির্দিষ্ট চাকুরীর জন্য নির্দিষ্ট সিট বরাদ্দ আছে। এখন শুধুমাত্র ঐ চাকুরী পাওয়াকে যদি জীবনের সফলতা মানেন তাহলে এই সংজ্ঞায় আমরা অনেকেই ব্যর্থ মানুষ। তাই নয় কি?
এই একই যুক্তি খাটে গাড়ি-বাড়ি ও নারীর ক্ষেত্রেও (নারীদের ক্ষেত্রে নর)। আমরা সবাই সব পাবো না যদি আমরা এই অনুকরণ শিল্পে মত্ত থাকি। এখন জিরার্দের ধারণা অনুযায়ী, যেহেতু আমরা সবাই সফল হতে পারলাম না সুতরাং আমরা যে ব্যর্থ হলাম সেজন্য আমাদের একটা ঠিকঠাক ‘বলির পাঠা’ দরকার। যে সমাজে অনুকরণ বেশি সে সমাজে ব্যর্থতার দায় দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ‘বলির পাঠা’ -ও উপস্থিত থাকে। আর এটাকেই জিরার্দ সুন্দর করে বলেছেন ‘Scapegoating Mechanism’।
জেরার্দ এই তত্ত্বে আরো বলছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্ম হয় বলির পাঠা বানানোর জন্য। “আমি ব্যর্থ” – এর দায়ভার বহন করার জন্য। কারণ মানুষের মধ্যে অনুকরণ যত বাড়বে ততবেশি ব্যর্থ হবে ও হতাশা বাড়বে। এবং, হতে পারে যারা এই অনুকরণে সফল তাদের দেখে বাকিদের ঈর্ষা ও হিংসা হতে শুরু করবে। ফলে সমাজে একধরণের সংঘর্ষ ও সহিংসতা লেগেই থাকবে। ধর্মের কারণে আমরা এই দায় দিতে পারি ঈশ্বর/আল্লাহ্’র কাছে অথবা, ভাগ্য/তকদীরের কাছে।
আমি ব্যর্থ হয়েছি কারণ আমার ভাগ্যে বা তকদীরে ছিলো না। আমি ব্যর্থ হয়েছি কারণ উপর আল্লাহ্ চান নাই। এইভাবে নিজের ব্যর্থতার দায় ঈশ্বর/আল্লাহ্ বা ভাগ্য/তকদীর কে দিয়ে একরকম সহিংসতা ও সংঘর্ষ থেকে সমাজ মুক্তি পেতে পারে। জেরার্দের মতে, এজন্যই সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতি আমাদের সামনে এনেছিলো।
যদিও জেরার্দের এই ‘মিমেটিক তত্ত্ব’ ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত তবুও এই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা কম হতে পারে না। অনেকের মতে, জেরার্দ এই ধরণের তত্ত্বের মাধ্যমে পুরো বিষয়টিকে সরলীকরণ করেছেন। কিন্তু সমালোচিত এই তত্ত্বের পুরোটাই ফেলে দেওয়া আজও সম্ভব নয়।