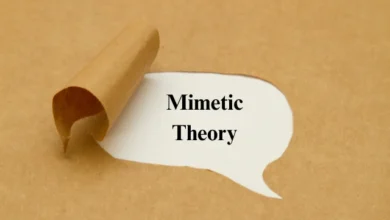মানুষ কেন নিজেদের অন্যদের সাথে তুলনা করে: মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ
লিওন ফেস্টিঙ্গারের সোশ্যাল কমপারিজন থিওরি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব
আমরা কেন নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করি? আমরা জানি নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করার মধ্যে বিশেষ কোন অর্থ নাই। আমরা আরো জানি, আমরা কেউ-ই হুবহু একইরকমের নই। আমরা সবাই আলাদা-আলাদা। কিন্তু তারপরেও ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমরা নিজেদের অন্যদের সাথে কেন তুলনা করে থাকি?
মানুষ যখন নিজেদের অন্যদের সাথে তুলনা করা শুরু করবে তখন তার মধ্যে অখুশি হবার প্রবণতা বাড়তে শুরু করবে। উদাহরণস্বরূপ: আমাদের সৌন্দর্য, আমাদের সম্পদ ও সম্পত্তি, আমাদের দক্ষতা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের যাবতীয় অর্জন প্রায় প্রায় আমরা অন্যদের সাথে তুলনা করে থাকি।
সমস্যা হলো, আমরা সবসময় আমাদের চেয়ে ভালো সংস্করণ খুঁজে পাবো এবং হতাশ হবো। কারণ আমাদের চেয়ে যিনি ভালো তাকে দেখে আমাদের মনে এক ধরণের হীনমন্যতা কাজ করতে পারে, ঈর্ষা কাজ করতে পারে।
কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসে তুলনা করার ইতিহাস শুরু থেকেই। আব্রাহামিক ধর্মে, আমাদের আদিম পিতামাতা আদম ও হাওয়া (আঃ) যখন তাদের সন্তানদের বিয়ের কথা ভেবেছেন সেখানেও তুলনা করার বিষয়টি এসে দাঁড়ায়। তাঁদের প্রতিটি মিলনে প্রতিবার এক জোড়া করে সন্তান জন্ম নিত। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। এই পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিয়ে হয়। এভাবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
কাবিল চেয়েছিলেন তার নিজের সুন্দরী বোনকে বিয়ে করতে, কিন্তু আল্লাহ্’র আইন অনুযায়ী সেটি নিষিদ্ধ ছিল। হাবিল যখন ধর্মীয় নিয়ম মেনে সেই বিয়ের অধিকার পেলেন, তখন কাবিল ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাইকে হত্যা করলেন। এই পুরো ঘটনাকে বিভিন্নভাবে যথাক্রমে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং মুসলিমরা ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু মূল বক্তব্য হচ্ছে, সৌন্দর্যের মাপকাঠি নির্ণয় করা হয়েছে এই দুই বোনের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে। আর এই তুলনা থেকেই ঈর্ষা ও হত্যার কান্ড ঘটেছে।
সুতরাং তুলনা করার ইতিহাস আমাদের সৃষ্টির শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিলো। এখন প্রশ্ন হলো, তুলনা করা যদি এত খারাপ হয় তাহলে আমরা কেন নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করে থাকি? মানুষের মধ্যে এই তুলনা করার যে প্রবণতা বিদ্যমান সেটা আমাদের জন্য ক্ষতি ডেকে আনছে। বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষও তো জানেন ১+১ = ২ কখনই হয় না। কারণ পৃথিবীতে একই রকমের দুটি বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তাহলে কেন আমরা এই অযৌক্তিক ‘তুলনা’ করে থাকি?
এই বিষয়ে জানতে আমাদের এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে। ১৯৫৪ সালে একজন বিখ্যাত আমেরিকার সামাজিক মনোবিজ্ঞানী লিওন ফেস্টিঙ্গার (Leon Festinger) আমাদের একটি তত্ত্ব উপহার দেন। এই তত্ত্বের নাম হচ্ছে, ‘সোশ্যাল কমপারিজন থিওরি (Social Comparison Theory)’।
তিনি জানান দুটো কারণে আমরা তুলনা করে থাকি,
১. ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করেন সেখানে অনিশ্চয়তা কমানোর জন্য বাকিদের সাথে নিজের তুলনা করেন।
২. তুলনা করার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।
ফেস্টিঙ্গার জানান, মানুষ কখনই স্বাধীনভাবে নিজেকে পর্যালোচনা করতে পারেন না। যখন লাখ টাকার প্রশ্ন আমাদেরকে করা হয় যে, “তুই কোন ক্ষেতের মূলা?” তখন আমরা অন্যদের দিকে তাকাই এবং নিজেকে তাদের তুলনায় পর্যালোচনা করে উত্তর দিয়ে থাকি। আমাদের আইডেন্টিটি বা পরিচয় প্রশ্নে আমরা জানিনা আমরা আসলে কে? আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমাদের জীবনে কি করা উচিত? বা, আমরা কতটুকু ভালো বা খারাপ? এই সবকিছু আমরা নির্ণয় করে থাকি অন্যদের সাথে নিজেকে তুলনা করার মাধ্যমে।
ফেস্টিঙ্গারের এই ধারণা ছিলো মনোবিজ্ঞানের অনেক বড় একটি অবদান। তবে এটুকু বলেই ফেস্টিঙ্গার তার তত্ত্ব শেষ করেন নাই। তিনি আরো একটু এগিয়ে গেছেন এবং পুরো বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন।
আমরা মোটামুটি কি কি বিষয় অন্যদের সাথে তুলনা করে থাকি?
১. আমাদের মতামত ও ২. আমাদের দক্ষতা
ফেস্টিঙ্গার বলেছেন, মানুষ স্বভাবগতভাবে নিজের মতামত এবং দক্ষতা মূল্যায়ন করতে চায়। যখন কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার মতো বাহ্যিক মাপকাঠি (যেমন পরীক্ষার নম্বর) থাকে না, তখন মানুষ অন্যদের সাথে তুলনা করে নিজের অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করে।
উদাহরণস্বরূপ:
১. মতামত: জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আপনার ধারণা সঠিক কিনা তা জানতে আপনি অন্যদের মতামতের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন। নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি কি এই সংকটে সঠিক অবস্থানে আছি?
২. দক্ষতা: আপনি দিনে কত ঘন্টা কাজ করছেন, তা অন্যদের কাজের সময়ের সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন করতে পারেন। মানে আপনি পরিশ্রমী নাকি অলস?
ফেস্টিঙ্গারের তত্ত্ব অনুযায়ী, সামাজিক তুলনা মূলত দুটি ধরনের হতে পারে:
১. উর্ধ্বমুখী তুলনা (Upward Comparison): যারা আপনার চেয়ে বেশি দক্ষ বা সফল, তাদের সাথে নিজেকে তুলনা। উদাহরণ: কোনো প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীকে দেখে নিজের প্রস্তুতি বাড়ানো।
২. অধোমুখী তুলনা (Downward Comparison): যারা আপনার চেয়ে কম সক্ষম, তাদের সাথে নিজেকে তুলনা। উদাহরণ: চাকরি হারানোর পর যারা আরও খারাপ পরিস্থিতিতে আছে, তাদের কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করা।
প্রথম ধরণের তুলনা আমরা করে থাকি আমাদের নিজের উন্নতির জন্য বা প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য এবং দ্বিতীয় ধরণের তুলনা আমরা করে থাকি আমাদের নিজেদের সন্তুষ্ট রাখতে বা সান্ত্বনা দিতে।
বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই তুলনার নেতিবাচক প্রবণতা বহুগুণ বেড়েছে। ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে অন্যদের সুখী, সফল জীবন দেখে হতাশা বা হীনমন্যতা তৈরি হতে পারে। আবার অন্যের দুর্দশার খবর দেখে নিজের জীবন নিয়ে কৃতজ্ঞতা বোধ করা বা শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। অথচ আমরা জানি, মিডিয়ায় মানুষের জীবনকে ‘পরিপূর্ণ/পারফেক্ট’ হিসেবে দেখানো হয়, যা প্রায়শই বাস্তবের চেয়ে ভিন্ন। এতে করে আমাদের ব্যক্তি পর্যালোচনায় ভুল হতে পারে।
তিনি তার গবেষণায় গ্রুচো মার্কস ফ্যান ক্লাবের একটি উদাহরণ দেন। যখন ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তখন তারা একে অপরের সাথে আলোচনা করে বা নিজের মত পরিবর্তন করে ঐক্য বজায় রাখে। এটি দেখায়, সামাজিক চাপ মানুষের তুলনা ও আচরণকে প্রভাবিত করে।
ফেস্টিঙ্গারের তত্ত্ব অনুযায়ী, তুলনা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এটি আজ অতিরিক্ত মাত্রা পেয়েছে। এই তুলনা ইতিবাচক প্রেরণা দিতে পারে আবার হতাশাও তৈরি করতে পারে। তাই, অন্যদের সাথে তুলনার সময় বাস্তবতা এবং নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝে এগোনো জরুরী।
আরো ভালো হয়, নিজের যে কাজটা করতে ভালো লাগে সেখানে শতভাগ প্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ করে যাওয়া এবং কোনোভাবেই নিজেকে অন্যদের সাথে সরাসরি তুলনা করে নিজেকে ছোট করা যাবে না।